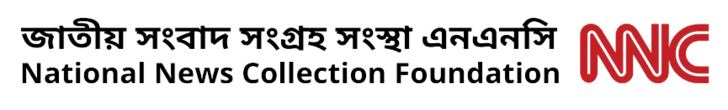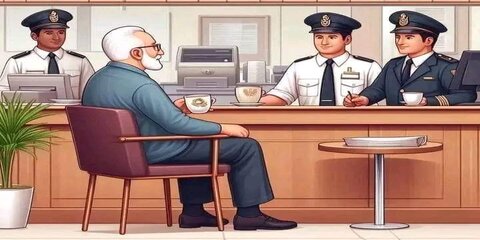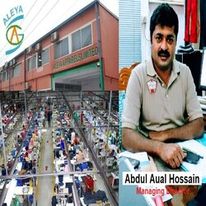পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ কোনো সাংবাদিককে তলব করতে চাইলে, তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট আইনি ও সাংবিধানিক বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। নিচে এ বিষয়ে আইনি ভিত্তি ও যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা করা হলো:
১. সংবিধানিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নাগরিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী:
প্রত্যেক নাগরিকের বাক্-স্বাধীনতার অধিকার আছে।
সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে, তবে কিছু যৌক্তিক বিধিনিষেধ প্রযোজ্য (যেমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, পর্নোগ্রাফি, আদালত অবমাননা ইত্যাদি)।
২. তথ্যসূত্র প্রকাশে বাধ্য করার বৈধতা
সাংবাদিকতার নৈতিক ও পেশাগত নীতিমালায় সাংবাদিকরা সাধারণত তাদের তথ্যসূত্র গোপন রাখার অধিকার রাখে। বাংলাদেশে এখনো “জার্নালিস্ট প্রোটেকশন ল’” বা “শিল্ড ল’” স্পষ্টভাবে নেই, তবে নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণগুলো বিবেচ্য:
সাংবাদিকের তথ্যসূত্র প্রকাশে বাধ্য করার জন্য আদালতের নির্দেশ প্রয়োজন। পুলিশের একতরফাভাবে তলব করে তথ্যসূত্র জানতে চাওয়ার আইনগত ভিত্তি দুর্বল, বিশেষ করে যদি তা কোনো তদন্ত বা ফৌজদারি মামলার অংশ না হয়।
সাংবাদিক যদি কোনো অপরাধে সরাসরি জড়িত না থাকেন, শুধুমাত্র সংবাদ প্রকাশের জন্য তাকে তলব করা সংবিধান পরিপন্থী ও হয়রানিমূলক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
৩. তদন্তের প্রয়োজন হলে কীভাবে সাংবাদিককে যুক্ত করা যায়
যদি পুলিশ মনে করে যে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে একটি অপরাধের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে, তবে পুলিশ তদন্ত শুরু করতে পারে।
তদন্তের অংশ হিসেবে সাংবাদিকের সহায়তা চাওয়া যেতে পারে, তবে তা হওয়া উচিত সম্মানজনক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক ভিত্তিতে, জোরপূর্বক বা হয়রানিমূলক না।
৪. আইনি উদাহরণ
কিছু দেশে, যেমন ভারত বা যুক্তরাষ্ট্র, তথ্যসূত্র প্রকাশে সাংবাদিকদের বাধ্য করা হলে আদালতের অনুমতি বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রয়োজন হয়।
বাংলাদেশেও উচ্চ আদালতের রায়ে বারবার বলা হয়েছে, সাংবাদিকদের পেশাগত স্বাধীনতা এবং তথ্যসূত্র রক্ষা করার অধিকারকে সম্মান জানাতে হবে।
সংক্ষেপে, পুলিশের সরাসরি তলব করার কোনো শক্তিশালী আইনি ভিত্তি নেই যদি না:
বিষয়টি কোনো ফৌজদারি মামলার তদন্তের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং আদালতের অনুমতি বা পরোয়ানা থাকে।